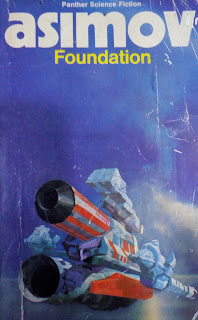আশি বছর আগের এক
প্রবন্ধগুচ্ছঃ প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা
গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়
দু’বছর
আগে চলে গেল মেঘনাদ সাহার জন্মের একশো পঁচিশ বছর। এবছর আমরা তাঁর নামাঙ্কিত সমীকরণের
শতবর্ষ পালন করছি। মেঘনাদ সাহা শুধু বিরাট বিজ্ঞানী ছিলেন না, দেশ ও সমাজ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং দেশের ও মানুষের উন্নতিতে সক্রিয়ভাবে
অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৯৩৯-৪০ সালে একগুচ্ছ
প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, যেগুলি আজও প্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষ পত্রিকাতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলিতে
মেঘনাদ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন।
এই লেখাতে আমরা সেগুলির দিকে ফিরে তাকাব।

এই রচনাগুলির একটা
প্রেক্ষাপট আছে। সুভাষচন্দ্র ও নেহরুর সঙ্গে দেশের উন্নতি বিষয়ে কাজের জন্য মেঘনাদের
যোগাযোগ হয়েছিল। স্বাধীনতার সময় অবশ্য দেশের বিজ্ঞানের পথ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে জহরলালের
মতের মিল হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু হোমি জাহাঙ্গির ভাবার কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে কেন্দ্রীয়
বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ার উপর জোর দিয়েছিলেন; তাঁর সেই বিখ্যাত Temples of
Modern India-র মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলিও পড়বে। মেঘনাদের মত ছিল গবেষণার মূল কেন্দ্র
হওয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয়। সারা পৃথিবীতেই বিশ্ববিদ্যালয়ই গবেষণার মূল কেন্দ্র; অনেকেই
মনে করেন নেহরুর নীতি অনুসরণের ফলে আমাদের দেশে বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ ব্যাহত হয়েছে।
কিন্তু সে অনেক পরের কথা।
অনেক আগে থেকেই দেশের ভবিষ্যৎ বিকাশ বিষয়ে কংগ্রেসের মূল অংশের
দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মেঘনাদের তীব্র আপত্তি ছিল। গান্ধীজীর চিন্তাধারা অনুসরণ করে কংগ্রেস মনে করত চরকা ও কুটিরশিল্পই দেশের বিকাশের একমাত্র পথ। মেঘনাদের মত ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সোভিয়েত ইউনিয়নের
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চোখ-ধাঁধানো সাফল্য সেই মুহূর্তে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া দেশকে এগোনোর পথের দিশা দেখাচ্ছে। সোভিয়েত মডেলের একটা
মূল কথা ছিল বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে পরিকল্পনামাফিক ব্যাপক অংশের জনগণের
উন্নয়ন; শুধু মেঘনাদ নয়, সারা পৃথিবীতে অনেক চিন্তাবিদই তাতে প্রভাবিত হয়েছিলেন।
মেঘনাদের শিক্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন যে একটা
দেশ কত এগিয়ে, তা তার সালফিউরিক অ্যাসিড ও ইস্পাত তৈরির পরিমাণ থেকে বোঝা যায়। প্রফুল্লচন্দ্র নিজে রসায়ন শিল্পের উন্নতিকল্পে বেঙ্গল
কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। পক্ষান্তরে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসি
মন্ত্রীসভার শিল্পমন্ত্রী কৈলাসনাথ কাটজু একটা দেশলাই বানানোর কারখানার উদ্বোধন করে
দেশ শিল্পের পথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, এ কথা জেনে মেঘনাদের মনে হল দেশের
বিশাল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য ভারি শিল্পের
প্রয়োজনীয়তা কংগ্রেসকে বোঝাতে হবে।
১৯৩৮ সালে
কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র, তাঁর সঙ্গে মেঘনাদের ভালোই যোগাযোগ ছিল।
১৯২২ সালে অবিভক্ত
বাংলাতে যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, মেঘনাদ ছিলেন তার ত্রাণ কমিটির সম্পাদক। সুভাষচন্দ্র কমিটির পক্ষ থেকে ত্রাণ নিয়ে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গে। সে বছরই সুভাষচন্দ্রের আমন্ত্রণে মেঘনাদ বঙ্গীয় যুবক সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র
কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পরেই মেঘনাদ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তাঁরই পরামর্শে সোভিয়েত
মডেলের অনুসরণে সুভাষচন্দ্র তৈরি করলেন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি।
একটা কথা বলে রাখা ভালো, মেঘনাদ যে রাশিয়ার পদ্ধতি হুবহু ভারতে চালাতে চেয়েছিলেন, তা নয়। শান্তিনিকেতনে এক বক্তৃতার
কথায় আমরা এখনি আসব, সেখানে জাতীয় পরিকল্পনা প্রসঙ্গে মেঘনাদ বলেছিলেন, ‘এই প্রকার দেশব্যাপী শিল্পপরিকল্পনা
রুশিয়ার পরিকল্পনা নহে। যদি কোনো আদর্শকে ফলবান করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে কেবল
বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়। রুশিয়ার বর্তমান জাতীয় জীবন খানিকটা
অপূর্ণ, কারণ এখানে আদর্শে ও কার্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব। যদি
আমরা আমাদের সভ্যতার উৎসকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের জীবনাদর্শকে
সামাজিক মৈত্রী, সার্বজনীন প্রীতি ও নৈতিকতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।’
দিল্লিতে কংগ্রেস কমিটির মিটিঙে একদিন পরে পৌঁছেছিলেন
মেঘনাদ; আগের দিনই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বেশ্বরাইয়া। কিন্তু মেঘনাদ তাতে সন্তুষ্ট হতে
পারলেন না, তাঁর মনে হল কমিটির শীর্ষে কোনো প্রধান রাজনৈতিক নেতা না থাকলে তার সুপারিশের কোনো মূল্য থাকবে না। তাঁর অনুরোধে বিশ্বেশ্বরাইয়া জহরলাল
নেহরুর সমর্থনে সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়াতে রাজি হলেন।
প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি
হওয়ার জন্য জহরলাল নেহরুকে অনুরোধ করলেন মেঘনাদ। তিনি রাজি হলেও সাহার সন্দেহ গেল
না, নেহরুর পক্ষে বাস্তবে গান্ধীজীর প্রভাবকে
অগ্রাহ্য করা কঠিন। তাই এমন একজনের শরণাপন্ন হলেন যাঁর কথা গান্ধী বা নেহরু কেউই সহজে
উড়িয়ে দিতে পারবেন না। ১৯২১
সালে জার্মানিতে তাঁর সঙ্গে
রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল, কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ
জানিয়েছিলেন। সতের বছর পরে সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করার সময় হল। রবীন্দ্রনাথও দেশের
উন্নয়ন বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হলেন, জহরলালকে চিঠি দিলেন।
এই বক্তৃতাটি ‘একটি নতুন জীবন
দর্শন’ এই শিরোনামে
ভারতবর্ষ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। মেঘনাদ বলেছিলেন, ‘এই জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকে বলেন যে আমাদিগকে শহর হইতে গ্রামে প্রত্যাবর্তন
করিয়া কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। একটু ভাবিয়া
দেখিলে এই সমস্ত যুক্তির অসারতা বুঝা যায়।’ তিনি আরও বলেছিলেন,
‘আমাদিগকে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো যান্ত্রিক সভ্যতায়
শ্রেষ্টত্বলাভ করিতে হইবে। ভারতের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, তাঁহারা বলেন যে
ভারতবর্ষের পক্ষে চিরকাল কৃষিপ্রধান হইয়া থাকা উচিত। এই মত অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক
বলিয়া মনে করি। যদি আমরা সকলেই গ্রাম্য জীবনে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে মুষ্টিমেয়
পুঁজিবাদীদের পক্ষে শোষণ করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।’ নাম না করে গান্ধীজীর সমালোচনা এখানে স্পষ্ট। অনেক পরে
১৯৫১ সালে তিনি যখন লোকসভা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ভাবেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে
যে দলের বহুদিনের যোগ সেই কংগ্রেসের কাছেই প্রথম গিয়েছিলেন। কংগ্রেস শর্ত দেয় যে গান্ধীজীর চরকা ও কুটির শিল্পনীতিকে তিনি বিজ্ঞানবিরোধী ও পশ্চাৎমুখী বলেছেন, সেই কথা তাঁকে প্রত্যাহার করতে হবে।
সে কথা মেনে না নিয়ে তিনি বামপন্থীদের সমর্থনে প্রথম লোকসভাতে উত্তর কলকাতা কেন্দ্র
থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন।
লেখা প্রকাশের পরে যে
পরিস্থিতি সৃষ্টি হল তার থেকেই আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধগুচ্ছের জন্ম; শান্তিনিকেতনের বক্তৃতাটিকে সেগুলির প্রাক-কথন বলা যেতে পারে। পুরো প্রবন্ধটি পড়লে স্পষ্টতই বোঝা
যায় যে এটি গান্ধীজীর নীতির সমালোচনা। কিন্তু গান্ধীবাদীদের নয়, হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে
বিশ্বাসীদের আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন মেঘনাদ। কেন এই লেখা তাঁদের গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল?
১৯৩৭ সালে এক প্রবন্ধে
মেঘনাদ লিখেছিলেন, ‘পশ্চিমা
জাতিগুলি চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে যে কদাচিৎ কখনও দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ
প্রভৃতি বিপর্যয় ঘটিলেও পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি অক্ষুণ্ণই আছে। এই বিশ্বাসই
চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে তাহাদের অত্যাশ্চর্য সাফল্যের মূলে।’ এখানে মেঘনাদ একটু
অত্যুক্তি করেছিলেন সন্দেহ নেই, পাশ্চাত্যের জাতিরাও চিরকাল প্রগতির ধারণাতে বিশ্বাসী
ছিল না। মধ্যযুগে তারাও বিশ্বাস করত যে নতুন কিছু জানার নেই, সবই প্রাচীন পণ্ডিতরা
বলে গেছেন। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার তাই মানুষের চিন্তার ইতিহাসেও এক যুগান্তকারী
ঘটনা, প্রাচীন গ্রিক বা রোমানদের লেখায় সেই নতুন মহাদেশের কথা ছিল না। ইউরোপীয় ভাষাসমূহে
‘ডিসকভারি’ বা সমার্থক শব্দগুলির ইতিহাস সেই পরিবর্তনের সাক্ষী।
প্রগতির
ধারণার সূত্র ধরেই মেঘনাদ শান্তিনিকেতনে বলেছিলেন, ‘আদর্শই সভ্যতার গতি নির্ণয় করে এবং প্রথম হইতেই আদর্শের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ
করিতে পারিলে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে। ... প্রত্যেক সভ্যতার আদর্শের ভুল ত্রুটি
আছে এবং বর্তমানে সমস্ত প্রাচীন ধর্মাত্মক আদর্শই অসম্পূর্ণ বলিয়া
প্রতিপন্ন হইয়াছে। কারণ এই সমস্ত ধর্ম তথা আদর্শ বিশ্বজগতের যে ধারণার উপর
প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণা নিছক কল্পনামূলক। … প্রায় সকল প্রাচীন ধর্মেই কল্পিত
হইয়াছে যে, পূর্বে এক সত্যযুগ ছিল, তখন মানুষ পরস্পর সম্প্রীতি-সূত্রে বাস করিত।
এবং তাহাদিগকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ভুগিতে হইত না। এখন আমরা জানি যে, এইরূপ
সত্যযুগের ছবি ভ্রমাত্মক।’ তার আগে বলেছিলেন, ‘হিন্দুর সৃষ্টিকর্তা
একজন দার্শনিক। তিনি ধ্যানে বসিয়া প্রত্যক্ষ জগত, স্থাবর ও জঙ্গম, জীব এবং ধর্মশাস্ত্রাদি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য যাঁহারা মাথা খাটায়, অলস দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করে এবং নানারূপ রহস্যের কুহেলিকা সৃষ্টি করে, হিন্দু সমাজে তাহাদিগকে খুব বড়ো স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী, কারিগর ও স্থপতির স্থান এই
সমাজের অতি নিম্নস্তরে এবং হিন্দু সমাজে হস্ত ও মস্তিষ্কের পরস্পর কোনো যোগাযোগ নাই। তাহার ফল হইয়াছে এই যে সহস্র বছর ধরিয়া হিন্দুগণ শিল্প ও
দ্রব্যোৎপাদনের একই ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং তজ্জন্য বহুবার
যান্ত্রিক বিজ্ঞানে উন্নততর বৈদেশিকের পদানত হইয়াছে।’
মেঘনাদের লেখার উপরে এখানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের
‘A History of Hindu Chemsitry’-এর প্রভাব স্পষ্ট। প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছিলেন, ‘In
ancient India the useful arts and sciences, as distinguished from mere
handicrafts, were cultivated by the higher classes.... unfortunately a
knowledge of these perished with the institution of the caste system in its
most rigid form.’ পরে মেঘনাদ তাঁর বক্তব্যকে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন,
সে কথায় আমরা ফিরে আসব।
স্বাভাবিক ভাবেই মেঘনাদের এই প্রবন্ধের বহু
সমালোচনা হয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল পন্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রমের অনিলবরণ রায়ের লেখাটি।
সেটিও ভারতবর্ষ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। অনিলবরণ অভিযোগ করেছিলেন মেঘনাদ হিন্দুর দর্শন, ধর্ম ও ভারতের
ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানার কোনো চেষ্টা না করে পাশ্চাত্য সমালোচকদের
মামুলি কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত উল্লেখ করতে অনিলবরণ বোঝাতে
চান যে ভগবান একাধারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; চার বর্ণের মধ্যে
প্রাচীন সমাজে কেউই ন্যূন ছিল না। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র জগৎ সম্পর্কে
যে কথা বলা হয়েছে, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাকেই সমর্থন করে। ‘বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে এই বিশ্ব জগতের পশ্চাতে
একটা বিরাট চৈতন্য রহিয়াছে,’ মেঘনাদ এ বিষয়ে
গত শতাব্দীতে পড়ে আছেন। বিবর্তন, সূর্যকেন্দ্রিক জগৎ ইত্যাদি আধুনিক মত প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে
পাওয়া যায়। শেষে তিনি লেখেন “ডক্টর মেঘনাদ সাহা
যদি বিজ্ঞানের আধুনিকতম জ্ঞান লইয়া দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করেন যে উহার সহিত হিন্দুর
প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার কোনই বিরোধ নাই, তাহা হইলেই তাহার ন্যায় প্রতিভাশালী
ব্যক্তির উপযুক্ত কর্ম করা হইবে এবং তিনি দেশের এবং জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করিতে
পারিবেন।’
অসুস্থতার
কারণে এই লেখাটি কিছুদিন মেঘনাদের চোখে পড়েনি। তিনি ছোটবেলা থেকে জাতিভেদ প্রথা ও দারিদ্রের
শিকার। কলকাতার নাগরিক সমাজেও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত তরুণ মেঘনাদ নানা সময়ে ব্যঙ্গের শিকার
হয়েছেন। নিজের কৃতিত্বে তিনি বিশ্বের দরবারে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও
বিদেশী বিজ্ঞানীদের মুরুব্বিয়ানার মনোভাবও তাঁকে আহত করত। শৈশব-কৈশোর-প্রথম যৌবনের
সেই অবহেলা ও অপমান তাঁর মনে স্থায়ী দাগ কেটে গিয়েছিল। সমসাময়িকদের সাক্ষ্য থেকে তাঁর
মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। অনিলবরণ রায়ের উপদেশ দানের ভঙ্গি এবং জাতিভেদ প্রথার প্রতি সমর্থন
তাঁর পছন্দ হয়নি। ভারতবর্ষ পত্রিকাতে তিনি পরপর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে সেই সমালোচনাকে
ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। মোহিনীমোহন দত্ত ভারতবর্ষে একটি প্রবন্ধে মেঘনাদের কথার দুর্বলভাবে
উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন, অপর একটি প্রবন্ধে মেঘনাদ তাঁকে তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেন।
মেঘনাদের এই প্রবন্ধগুলিই আমরা সংক্ষেপে ফিরে দেখব।
প্রবন্ধগুলির
বিষয়বস্তুতে ঢোকার আগে বলতে হয় তাদের খরশান ব্যঙ্গের কথা। স্থানাভাবে একটিই উদাহরণ
দেখা যাক। সাহা লিখেছেন, জনৈক পরিচিত ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কী বৈজ্ঞানিক
কাজ করেছেন। মেঘনাদের কথা শুনে তিনি বলেন যে ‘সবই ব্যাদে আছে।’
বেদের কোথায় আছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে বেদ তাঁর পড়া হয়নি বটে, কিন্তু
তাঁর বিশ্বাস সবই সেখানে পাওয়া যাবে। প্রাচীন শাস্ত্র থেকে যাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজে বার করেন, তাঁদের সম্পর্কে মেঘনাদের এই ‘সবই ব্যাদে আছে’ ব্যঙ্গোক্তি আজ প্রবাদে
পরিণত।
মেঘনাদ লিখলেন সমালোচক তাঁর প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই বুঝতে পারেননি। তিনি দেখাতে
চেয়েছিলেন যে আদর্শ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়, ভগবানের ধারণাও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীনকালের
ভারতীয় সভ্যতা অন্যদের থেকে এগিয়ে ছিল কিনা তা আলোচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; সেই সময়ে
তা শ্রেষ্ঠ ছিল বলে আধুনিক যুগেও তা শ্রেষ্ঠ, এ কুযুক্তি। তা যে মধ্যযুগ বা আধুনিক
যুগের উপযোগী নয়, ইতিহাস পাঠ করলেই তা বোঝা যায়। অনিলবরণ লিখেছিলেন হিন্দুধর্ম ও দর্শনের
মূল হল বেদ। সাহা দেখান যে বৈদিক ধারার বাইরেও হিন্দু ধর্মের মধ্যে একটি বিরাট ও সুপ্রাচীন
ধারা বহমান।
অনিলবরণের জাতিভেদ প্রথার সমর্থন স্বভাবতই তাঁর সমালোচনার শিকার হয়েছে। পুরুষসূক্তের
আলোচনা প্রসঙ্গে মেঘনাদ মনে করিয়ে দেন যে সমস্ত বিশেষজ্ঞের মতেই সেটি পরবর্তীকালে রচিত,
জাতিভেদ প্রথার সমর্থনে বেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঋক বেদে অন্য কোথাও ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চার জাতির উল্লেখ নেই। জাতিভেদ
প্রথার দার্শনিক ব্যাখ্যা তাঁর প্রবন্ধের আলোচনাতে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, দেখতে হবে
সমাজ সেই প্রথাকে কেমনভাবে নিয়েছে। এই প্রথার থেকেই অস্পৃশ্যতা, বর্ণসঙ্করবাদ ইত্যাদি
কুপ্রথার উদ্ভব। তার থেকেও বড় কথা হল যে জাতিভেদ প্রথা হাত ও মাথার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন
করে দিয়েছে, ফলে নতুন প্রকৌশল সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। ‘ফলে বৈদিক যুগ হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত আমরা একই প্রাগ্বৈদিক চরকাতেই সুতা
কাটিতেছি, কাঠের তাঁতে বস্ত্রবয়ন করিতেছি এবং আধুনিককালেও মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে
পুনরায়, “বৈদিক অসভ্যতায়” ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন।’ মেঘনাদ আরও বলেন যে প্রতিভা থাকলে ইউরোপে কসাইয়ের ছেলে
শেক্সপিয়ার হতে পারত, আমাদের প্রাচীন সভ্যতায় সে সেইরকম চেষ্টা করলে তার মাথা কেটে
নেওয়ার বিধান আছে।
প্রবন্ধগুলিতে মেঘনাদ নানা বিষয় আলোচনাতে এনেছেন।
বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করে এবং জ্যোতির্বিদ্যার সাক্ষ্য থেকে ঋক বেদ রচনার কাল
নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। প্রাক-বৈদিক সভ্যতার দেবদেবীরা কেমনভাবে হিন্দু ধর্মের মধ্যে
স্থান পেয়েছে তা দেখিয়েছেন। জাতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান প্রযুক্তির
ভূমিকা তিনি এই লেখাতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কেমনভাবে ঘটে, বিজ্ঞানের
যুক্তি বলতে কী বোঝায় – এই সমস্ত নিয়ে একজন প্রথম শ্রেণির বিজ্ঞানীর মনোভাব প্রকাশ
পেয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় পঞ্জিকাতে ভুল থাকার ফলে কেমনভাবে আমাদের বছর গোনাতে ভুল রয়ে
গেছে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন; স্মরণীয় যে পরে তিনি স্বাধীন ভারতে পঞ্জিকা সংস্কারের দায়িত্ব
পেয়েছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রের ধারণার প্রতি বিদেশী বিজ্ঞানীদের বা আধুনিক বিজ্ঞানের
তথাকথিত সমর্থন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে মেঘনাদ দেখান যে তাঁর সমালোচকরা বিজ্ঞান
আদৌ বোঝেননি বা ভুল ব্যাখ্যা করছেন। দীর্ঘ প্রবন্ধগুলির সমস্ত দিক আলোচনা করা এই নিবন্ধের
পরিসরে সম্ভব নয়। এই লেখার
অবশিষ্ট অংশে আমরা শুধু সংক্ষেপে প্রাচীন শাস্ত্রের
ভিতর বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারের সন্ধান বিষয়ে তাঁর বক্তব্য দেখার চেষ্টা করব। বর্তমানে
যখন পুরাণ বা মহাকাব্যের মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজার চেষ্টা চলছে, পুষ্পক রথের মধ্যে প্রাচীন
বিমানের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তখন এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বিষয়টাকে কেমনভাবে দেখেছিলেন
সেই আলোচনা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।
মেঘনাদ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে
খুবই সচেতন ছিলেন, কিন্তু অযৌক্তিকভাবে ইতিহাসের সাক্ষ্য উপেক্ষা করে তার শ্রেষ্ঠত্ব
ঘোষণাতে তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি প্রথমেই লেখেন, ‘বর্তমান সমালোচকের মত অনেক সমালোচকই বোধহয় কল্পনা করিয়াছেন যে আমি হিন্দু
ধর্মের ও দর্শনের কোন মৌলিক গ্রন্থ পড়ি নাই। এরূপ ধারণা করিবার পূর্বে একটু
অনুসন্ধান করিয়া লইলে বুদ্ধিমানের কার্য হইত। যাহা হউক, আশা করি এই প্রত্যুত্তর পাঠে
তাঁহার ভ্রান্তির নিরসন হইবে।’ এরপরে তিনি বেদ, উপনিষদ, মহাভারত ও পুরাণ থেকে নানা উদাহরণ তুলে দেখান যে কীভাবে
সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করে প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধান করা হচ্ছে।
মেঘনাদ লিখলেন,
‘এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, বিজ্ঞান আর নূতন কি করিয়াছে? বিজ্ঞান বর্তমানে
যাহা করিয়াছেন তাহা কোন প্রাচীন ঋষি, বেদ পুরাণ বা অন্য কোথাও না কোথাও বীজাকারে বলিয়া গিয়াছেন।’ অনিলবরণ রায় লিখেছিলেন জন্মান্তরবাদ ও অবতারতত্ত্বই প্রমাণ
করে যে হিন্দুরা বিবর্তনবাদ জানত। মেঘনাদ প্রশ্ন করেন, জন্মান্তরবাদ বলে মানুষ পাপ
করলে মনুষ্যেতর জীব হিসাবে জন্ম হয়, তার সঙ্গে বিবর্তনের সম্পর্ক কোথায়? অবতারবাদ প্রসঙ্গে
তিনি দেখান যে মহাভারত, পুরাণের মধ্যে অবতারের তালিকার অনেক পার্থক্য আছে। অবতারবাদের
মধ্যে অনেক স্ববিরোধিতার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবতারবাদ থেকে অনিলবরণ যে অর্ধপশু-অর্ধমানুষ
বা বামন মানুষের কথা বলেছেন, তারা কোনোদিন পৃথিবীতে ছিল না। বিবর্তনবাদের সঙ্গে সভ্যতার
বিকাশকে সমালোচক গুলিয়ে ফেলে সত্যযুগ কলিযুগ ইত্যাদির কথা বলেছেন। বাস্তব পৃথিবীতে
কখনো সত্যযুগ ছিল না, তা একান্তই প্রাচীন পুরাণকারের কল্পনা।
অনিলবরণ লিখেছিলেন পৃথিবী যে গোল,
সূর্য যে সৌরজগতের কেন্দ্র ও পৃথিবী যে চলমান তা কোপার্নিকাস বা গ্যালিলিওর অনেক আগেই
ভারতবর্ষে জানা ছিল। মেঘনাদ মনে করিয়ে দেন যে গ্যালিলিও বা কোপার্নিকাসের অনেক আগে
থেকেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এই সমস্ত ধারণা ছিল। পৃথিবী যে চলমান সে কথা এই দুজনের কেউ
প্রথম বলেননি। খ্রিস্ট জন্মের সাড়ে পাঁচশো বছর আগে গ্রিসে অ্যানাক্সিম্যান্ডার পৃথিবীর
আহ্নিক গতির কথা বলে গিয়েছিলেন। পৃথিবীর বার্ষিক গতির কথা বলেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়
শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টার্কাস। ওই শতাব্দীতেই আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানী
এরাটোস্থিনিস প্রথম পৃথিবীর ব্যাস মেপেছিলেন। পৃথিবী যে গোল তা তার অনেক আগে থেকেই
নিশ্চয় গ্রিকদের জানা ছিল, তা না হলে তার ব্যাস মাপার প্রশ্ন ওঠে না।
মহাভারতের সাক্ষ্য থেকে মেঘনাদ
পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ভারতবর্ষে আসার কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তিনি দেখান যে মহাভারতে
বার, রাশিচক্র, পৃথিবীর আহ্নিক বা বার্ষিক গতির উল্লেখ নেই। মহাভারতের মতে পৃথিবী সমতল,
সুমেরু তার কেন্দ্রে অবস্থিত, সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করে। এ থেকে বোঝা যায় যে মহাভারত
সংকলনের সময় পৃথিবীর আকার, আবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে ভারতবর্ষে জানা ছিল না। ভারতবর্ষে
খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেই পাশ্চাত্য জ্যোতিষ প্রচলিত হয়, এবং ভারতীয় জ্যোতিষীরা
সেই অনুযায়ী পঞ্জিকা রচনা শুরু করেন। মেঘনাদ ভারতীয় জ্যোতিষ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা
করেন। সূর্যসিদ্ধান্ত ও বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা উদ্ধৃত করে তিনি দেখান যে খ্রিস্টিয়
পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় জ্যোতির্বিদরাই প্রাচীন ভারতীয় পঞ্জিকাকে অশুদ্ধ বলে ইউরোপ
থেকে আগত পঞ্জিকা ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছেন।
মেঘনাদ বলেন যে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় পৃথিবী সম্পর্কে গ্রিক মতও তাঁদের
কাছে পৌঁছেছিল। সূর্য যে সৌরজগতের কেন্দ্র, সে বিষয়ে যে শ্লোকটি অনিলবরণ উদ্ধৃত করেছিলেন,
মেঘনাদ দেখান যে তাতে পৃথিবী যে গ্রহ সে কথা বলা নেই। সেই শ্লোকে সূর্য যে সৌরজগতের
কেন্দ্র বলা হয়েছে, তা মেনে নিতে গেল কল্পনাকে অনেকদূর বাড়াতে হয়; এর সরল অর্থ হল সমস্ত
গ্রহের মধ্যে সূর্য সবচেয়ে উজ্জ্বল।
মেঘনাদের কালেও বলা হত, আজও হয়, যে আর্যভট্ট পৃথিবীর
সূর্য প্রদক্ষিণের কথা প্রথম বলেছিলেন। আর্যভট্টের যে শ্লোকটি তার সমর্থনে উদ্ধৃত করা
হয়, তার থেকে স্পষ্টতই দেখা যায় আর্যভট্ট আহ্নিক গতির কথাই বলেছেন। মেঘনাদ লিখেছেন
যে বার্ষিক গতির কথা কোনো ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতিষী বলেছেন জানা নেই, আর্যভট্ট নিজে
পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র ধরে নিয়ে গ্রহদের গতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।
একই রকমভাবে একটি কথা এখনও শোনা
যায়, ভাস্করাচার্য মাধ্যাকর্ষণের কথা বলেছিলেন, সুতরাং ‘নিউটন আর নূতন কি করিয়াছে?’
সমস্যা হল যে যাঁরা বলেন তাঁরা মাধ্যাকর্ষণ সূত্রটিও ভালো করে পড়েন নি। নিউটন শুধুমাত্র
পৃথিবীর আকর্ষণের কথা বলেন নি, সমস্ত বস্তু অন্য বস্তুকে যে বলে আকর্ষণ করে তার গাণিতিক
রূপ দিয়েছিলেন এবং তার সাহায্যে পৃথিবী ও অন্য গ্রহদের কক্ষপথ নিরূপণ করেছিলেন। মেঘনাদের
মতে, দেশে এমন অপবিজ্ঞান প্রচারকের অভাব নেই যাঁরা সত্যের নামে এমন নির্জলা মিথ্যার
প্রচার করছেন।
এই প্রবন্ধগুলি রচনার পরে আশি
বছর কেটে গেছে। ভাবলে দুঃখ হয় যে প্রবন্ধগুলি আজও প্রাসঙ্গিক; অপবিজ্ঞান প্রচারকরা
এখনও কুযুক্তির আশ্রয় নিয়ে চলেছেন। বেদ না পড়েই তাঁরা বেদের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রযুক্তির
সমস্ত আধুনিক আবিষ্কারকে খুঁজে পান, মহাকাব্য ও পুরাণের গল্পের মধ্যে শল্যচিকিৎসাকে
সন্ধান করেন। বিজ্ঞান মানসিকতার দিক থেকেও আমরা এখনো খুব বেশি এগোতে পারিনি। মেঘনাদ
লিখেছিলেন ‘আমাদের দেশে শতকরা ৯৯ জন পুরুষ, এবং ১০০ জন স্ত্রীলোক ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। … পঞ্জিকায় অন্ধবিশ্বাস জাতীয় জীবনের
দৌর্বল্যের দ্যোতক।’ সেই মাপকাঠিতে আমাদের জাতীয় জীবন
এখনও দুর্বল।
মেঘনাদের ভাষা জায়গায় জায়গায় বেশ
কঠোর, কিন্তু তার কারণও ছিল। সেই কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু।
বলেছিলেন, ‘আমি সনাতনীদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার বন্ধু যেমন বলতেন
ঠাট্টা করে, সবই “ব্যাদে আছে”, “বেদে আছে” এই মনোভাবটা অনেক সময়ে যদি নিদান করতে হয়
তাহলে মাঝে মাঝে শক্ত কথাই বলতে হয়।’ মেঘনাদ লিখেছিলেন, ‘বর্তমান লেখক বৈজ্ঞানিকের
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুর বেদ ও অপরাপর ধর্মের মূলতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন।
ইহাতে অবজ্ঞা বা অবহেলার কোন কথা উঠিতে পারে না।’ এই বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টির
অভাবই আমরা বোধ করছি। স্থানাভাবে মেঘনাদের লেখাগুলির অনেক দিকই অনালোচিত থেকে গেল,
পাঠককে মূল প্রবন্ধগুলি পড়তে অনুরোধ করি।
(মেঘনাদ সাহা ও অনিলবরণ রায়ের রচনার উদ্ধৃতিগুলি ও সত্যেন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিটি
শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা রচনা সংকলন’ থেকে নেওয়া হয়েছে।)
প্রকাশঃ সৃষ্টির একুশ শতক, শারদীয় ২০২০

 আমরা চলেছি ডাম্বুলা ছেড়ে আরও দক্ষিণে ক্যাণ্ডির পথে। পোলোন্নারুয়া বা অনুরাধাপুরার মত অত প্রাচীনত্বের ছোঁয়া না থাকলেও ব্রিটিশরা দেশটা দখল করার আগে ক্যাণ্ডি ছিল এদেশের শেষ স্বাধীন রাজধানী। আমাদের যাবার পথটাও বেশ সুন্দর। কিন্তু দারুণ গরম। এসি গাড়িতে বসেও সকলের কেন জানি না খুব হাঁস-ফাঁস অবস্থা। একটা মশলা বাগানে ঢুকেছিলাম। দেশটার নাম তো দারুচিনির দ্বীপ, তাই মশলা কিনব ভাবলাম সবাই। একজন গাইড ঘুরে ঘুরে আমাদের সব ভেষজ উদ্ভিদ আর মশলার গাছগুলো চেনাচ্ছিল, আর বার করছে আর টপাটপ কত সব ভেষজ গুণে ভরা জড়িবুটি কিনছে। গাইড আমাদেরও অনেক উৎসাহিত করল কিছু কেনার জন্য। টাকে চুল গজানো থেকে শুরু করে শরীরের যে কোন অংশে লোম তোলা, যাবতীয় রোগ নিরাময় করা, বার্ধক্য রোধ করা--- সব ঔষধই মজুত ছিল সে বাগানে। গৌতমের হাতের একটা অংশে ভেষজ তেল একফোটা লাগিয়ে, লোম তুলে দিয়ে, হাতেনাতে প্রমাণও দিল। গৌতম টাকে চুল গজানোর বিষয়ে সম্ভবত আগ্রহী ছিল, কিন্তু যা সব দাম শুনলাম তাতে মাথার ফাঁক ঢাকতে গিয়ে পকেট ফাঁকা হবার যোগাড়। বাগানের ছোটো ছো্টো ছাউনির ভেতর দেখি বিদেশীরা ঐ সব দুর্মুল্য তেল দিয়ে সারা শরীর মালিশ করাচ্ছে। নেংটি পরিয়ে, সাদা চামড়াগুলোর পিঠে চটাস চটাস থাপ্পড় কষিয়ে ভালই ব্যাবসা চলছে। একজন পঞ্চাশোর্ধ সাহেব আর তার তরুণী সঙ্গিনীর ওপর দেখি একটা ছাউনিতে চলছে এরকমই পরীক্ষা নিরীক্ষা। মনে মনে ভাবলাম এই বয়সে সাহেব হয়ত মালিশ করে বয়সটাকে কিছুদিন আটকাবে; কিন্তু তার সঙ্গিনী! অল্পবয়সীদের চামড়ায় ভেষজ বেশি তাড়াতাড়ি কাজ করবে। তখন তাকে যদি বায়ো কি তেয়ো মনে হয়? তবে যে সাহেবের পার্শ্ববর্তিনীটি নাতনি-সম ঠেকবে!
আমরা চলেছি ডাম্বুলা ছেড়ে আরও দক্ষিণে ক্যাণ্ডির পথে। পোলোন্নারুয়া বা অনুরাধাপুরার মত অত প্রাচীনত্বের ছোঁয়া না থাকলেও ব্রিটিশরা দেশটা দখল করার আগে ক্যাণ্ডি ছিল এদেশের শেষ স্বাধীন রাজধানী। আমাদের যাবার পথটাও বেশ সুন্দর। কিন্তু দারুণ গরম। এসি গাড়িতে বসেও সকলের কেন জানি না খুব হাঁস-ফাঁস অবস্থা। একটা মশলা বাগানে ঢুকেছিলাম। দেশটার নাম তো দারুচিনির দ্বীপ, তাই মশলা কিনব ভাবলাম সবাই। একজন গাইড ঘুরে ঘুরে আমাদের সব ভেষজ উদ্ভিদ আর মশলার গাছগুলো চেনাচ্ছিল, আর বার করছে আর টপাটপ কত সব ভেষজ গুণে ভরা জড়িবুটি কিনছে। গাইড আমাদেরও অনেক উৎসাহিত করল কিছু কেনার জন্য। টাকে চুল গজানো থেকে শুরু করে শরীরের যে কোন অংশে লোম তোলা, যাবতীয় রোগ নিরাময় করা, বার্ধক্য রোধ করা--- সব ঔষধই মজুত ছিল সে বাগানে। গৌতমের হাতের একটা অংশে ভেষজ তেল একফোটা লাগিয়ে, লোম তুলে দিয়ে, হাতেনাতে প্রমাণও দিল। গৌতম টাকে চুল গজানোর বিষয়ে সম্ভবত আগ্রহী ছিল, কিন্তু যা সব দাম শুনলাম তাতে মাথার ফাঁক ঢাকতে গিয়ে পকেট ফাঁকা হবার যোগাড়। বাগানের ছোটো ছো্টো ছাউনির ভেতর দেখি বিদেশীরা ঐ সব দুর্মুল্য তেল দিয়ে সারা শরীর মালিশ করাচ্ছে। নেংটি পরিয়ে, সাদা চামড়াগুলোর পিঠে চটাস চটাস থাপ্পড় কষিয়ে ভালই ব্যাবসা চলছে। একজন পঞ্চাশোর্ধ সাহেব আর তার তরুণী সঙ্গিনীর ওপর দেখি একটা ছাউনিতে চলছে এরকমই পরীক্ষা নিরীক্ষা। মনে মনে ভাবলাম এই বয়সে সাহেব হয়ত মালিশ করে বয়সটাকে কিছুদিন আটকাবে; কিন্তু তার সঙ্গিনী! অল্পবয়সীদের চামড়ায় ভেষজ বেশি তাড়াতাড়ি কাজ করবে। তখন তাকে যদি বায়ো কি তেয়ো মনে হয়? তবে যে সাহেবের পার্শ্ববর্তিনীটি নাতনি-সম ঠেকবে!
 বিকেল গড়িয়ে ক্যাণ্ডি পৌঁছোলাম। এবার গন্তব্য ক্যাণ্ডির বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ। ভিতরে আছে একটি স্বর্ণ-মন্দির, নাম শ্রী দালাদা মালিগাওয়া, যেখানে বুদ্ধের দাঁত সংরক্ষিত আছে।
বিকেল গড়িয়ে ক্যাণ্ডি পৌঁছোলাম। এবার গন্তব্য ক্যাণ্ডির বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ। ভিতরে আছে একটি স্বর্ণ-মন্দির, নাম শ্রী দালাদা মালিগাওয়া, যেখানে বুদ্ধের দাঁত সংরক্ষিত আছে। পরদিন রওনা দিলাম নুয়ারা এলিয়া অর্থাৎ আলোর শহরের দিকে, আরও দক্ষিণে পার্বত্য প্রদেশে। এই পাহাড়ি অঞ্চলটি চা চাষের জন্য সবচেয়ে অনুকূল। আমরা পথে এখানকার সবচেয়ে বড় টি এস্টেটগুলোর একটাতে ঢুকেছিলাম। সুন্দর সুন্দর মোড়কে চা রাখা বিদেশে রপ্তানির জন্য। আমরা সবাই চা কিনলামও। ক্যাণ্ডি এবং নুয়ারা এলিয়া, দুটোই পাহাড়ি এলাকায় বলে আবহাওয়াটা মনোরম। এই জায়গাটাকে বলে লিটল ইংল্যান্ড। সেখানে পাহাড়ের ঢালে সুন্দর একটা লেকের ধারে আমরা বেশ অনেকক্ষণ কাটালাম। লেকটার নাম লেক গ্রেগরি, জলে অনেক পর্যটক বোটিং, ওয়াটার স্কুটারিং করছে। লেকের সামনের সাজানো বাগানে বসে ওগুলো দেখে সময় কাটছিল ভালই। হঠাৎ দেখি অনির্বাণ আর ঝুলনের মধ্যে কী নিয়ে যেন তর্কাতর্কি হচ্ছে। ঝুলন চাইছে ওয়াটার স্কুটারে চড়তে, আর অনির্বাণ একেবারেই নারাজ। বলছে, এই বয়সে বউ হারাতে ও কোনমতেই রাজি নয়।
পরদিন রওনা দিলাম নুয়ারা এলিয়া অর্থাৎ আলোর শহরের দিকে, আরও দক্ষিণে পার্বত্য প্রদেশে। এই পাহাড়ি অঞ্চলটি চা চাষের জন্য সবচেয়ে অনুকূল। আমরা পথে এখানকার সবচেয়ে বড় টি এস্টেটগুলোর একটাতে ঢুকেছিলাম। সুন্দর সুন্দর মোড়কে চা রাখা বিদেশে রপ্তানির জন্য। আমরা সবাই চা কিনলামও। ক্যাণ্ডি এবং নুয়ারা এলিয়া, দুটোই পাহাড়ি এলাকায় বলে আবহাওয়াটা মনোরম। এই জায়গাটাকে বলে লিটল ইংল্যান্ড। সেখানে পাহাড়ের ঢালে সুন্দর একটা লেকের ধারে আমরা বেশ অনেকক্ষণ কাটালাম। লেকটার নাম লেক গ্রেগরি, জলে অনেক পর্যটক বোটিং, ওয়াটার স্কুটারিং করছে। লেকের সামনের সাজানো বাগানে বসে ওগুলো দেখে সময় কাটছিল ভালই। হঠাৎ দেখি অনির্বাণ আর ঝুলনের মধ্যে কী নিয়ে যেন তর্কাতর্কি হচ্ছে। ঝুলন চাইছে ওয়াটার স্কুটারে চড়তে, আর অনির্বাণ একেবারেই নারাজ। বলছে, এই বয়সে বউ হারাতে ও কোনমতেই রাজি নয়।